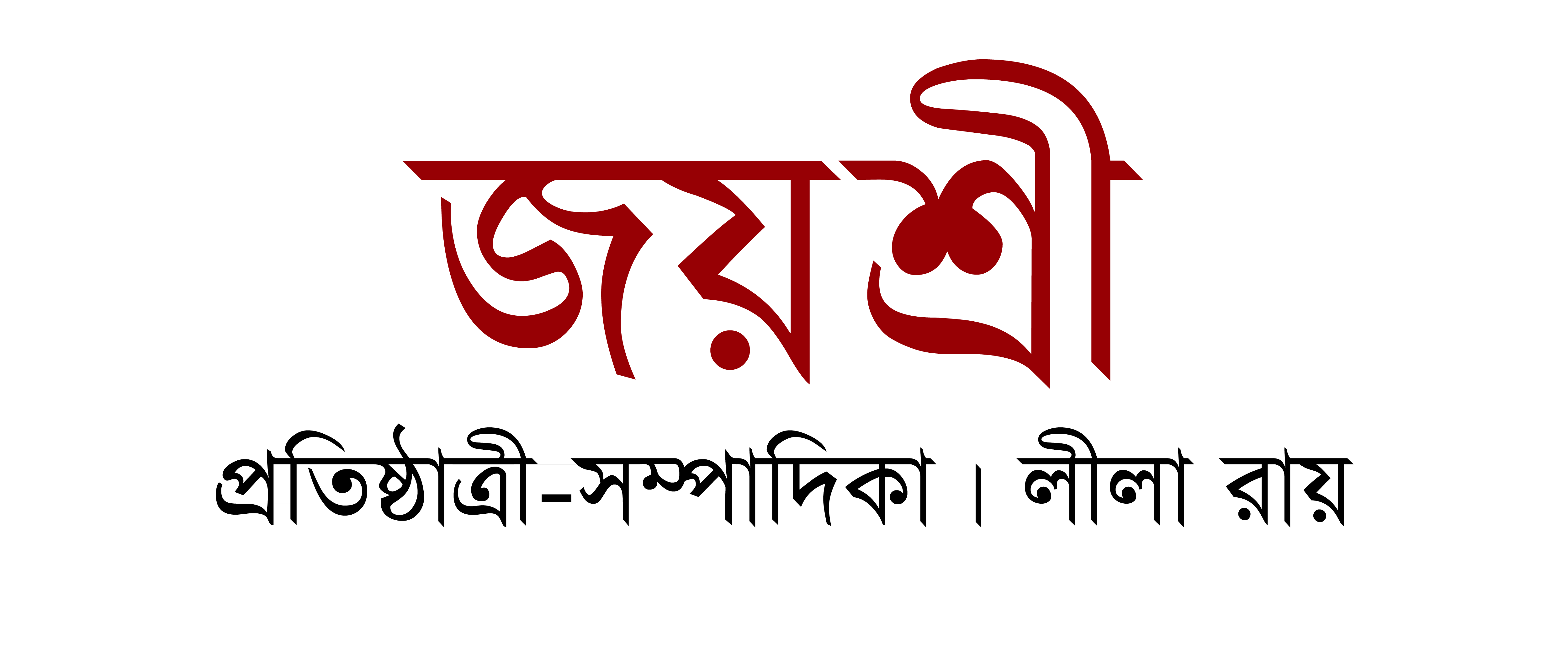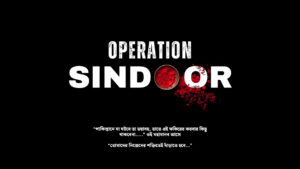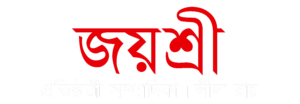বাংলাভাগের প্রস্তাব সমর্থনকারী ঐ ৫৮ জন সদস্যের নামের তালিকা আছে কার্যবিবরণীর সঙ্গে সংযোজিত তালিকায় (এপেন্ডিকস-বি) (পাতা-৮৫ থেকে ৮৭)। উক্ত এপেন্ডিকস-বি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই তালিকার ৮ নং নামটি হল জ্যোতি বসু এবং ১১নং নামটি রতন লাল ব্রাহ্মণের। প্রয়াত জননায়ক ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত কুমার বসুর নামও আছে তালিকায়- ৭ নম্বরে আর চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নাম ৯ নম্বরে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতা নিকুঞ্জবিহারী মাইতির নাম ১৭ এবং বিপ্লবী বীনা দাসের নাম ১৪ নম্বরে। ২৫ নম্বরে আছে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম; ২৭ নং এ কালীপদ মুখার্জির নাম ৩৫ নং এ নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নাম ৫৭ নং এ আছে কান্দির বিমল সিংহের। উল্লেখ্য ওই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ডি গোমস (৪০), এল আর পেন্টনি (৪৮) আর ই প্লেটেল (৪৯), মিসেস ই এম রিকেটস (৫৪) এবং জি চি ডি উইল্কস (৫৮) মতো সদস্যরাও ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। প্রস্তাবের বিপক্ষের ২১ জন সদস্যের নামের তালিকায় কোন অমুসলিম সদস্যে। অর্থাৎ ঐ ফলাফল হায়েছিল সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভাজনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভোট প্রদানে। আজ এ সত্য অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসকে অস্বীকারের নামান্তর। ওই বিবরণী থেকে কোনভাবে প্রতীয়মান হয় না যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত ছিলেন বঙ্গভঙ্গ করে হিন্দু প্রধান এলাকা ভারতে যোগদান প্রশ্নে ভোটাভুটিতে। সিপিআইএম এর অস্বস্তি হল ওই তালিকায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জ্যোতি বসু নাম থাকায়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে রাজনৈতিক দলের পক্ষেই হোক বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ও প্রায় আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সেদিনের রূঢ় বাস্তবতার ইতিহাস অস্বীকার বা বিকৃত করা কি অনৈতিক নয়।
কেহ বলেন মিথ্যা বলো, মিথ্যা প্রচার করো, কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো সত্যানুষ্ঠান করো। খআমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বলো, সত্যাচরণ করো, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে’-অনেককাল আগে বলা রবীন্দ্রনাথের কথাক’টি আবার মনে পড়ল সাম্প্রতিক এক রাজনৈতিক তরজার প্রেক্ষিতে।
‘পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড হিসেবে এবং অবস্থানগত বিপরীত স্থানে থেকেও জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণও ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন’ জুলাই এর গোড়ায় এক সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নবনির্বাচিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি মহাশয়ের এহেন মন্তব্যে এক নতুন বিতর্কের শুরুয়াত, অবশ্য যার মাধ্যমে সাধারণের সামনে এসেছে এক ঐতিহাসিক সত্য, যতই অপ্রিয় অস্বস্তিকর হোক কোন কোন মহলের পক্ষে। সত্যই ইতিহাস কথা কয়!
বাংলাভাগের জন্য দায় কার কিংবা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে কোন দিনটি উদযাপিত হওয়া উচিত এ নিয়ে চলা তরজার আবহে ঐ মন্তব্যে নতুন করে হাওয়া লেগেছিল বাদ-প্রতিবাদে কারণ এর সাথে কতিপয় মুখোশের বিদীর্ণজনিত অস্বস্তি তো আছেই। এবারের বিতর্কের সূচনা হয় সম্ভবত ‘ইতিহাসের বই থেকে ইতিহাস না পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ইতিহাস জানার ফল’ টিভির সান্ধ্যবিতর্কে অতি পরিচিত মুখ সিপিআইএম-এর যুবনেতার প্রকাশ্য সভা থেকে এমন কটাক্ষে। আবার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বড় হাউসের দৈনিকের একদা সম্পাদক মহাশয়ও প্রথমে এক ভিডিও প্রস্তুত করে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসুর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘যতদূর মনে পড়ে’র উল্লেখে বললেন ঐ তথ্য ভুল, কারণ বঙ্গীয় আইনসভায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু দিন দুই পরে তিনিই আবার ভিডিও করে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন যে ২০শে জুন ১৯৪৭ তারিখের তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভার কার্যবিবরণী থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মহ্মণ দু’জনেই অন্যন্য হিন্দু সদস্যের সঙ্গে বঙ্গবিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বিতর্ক থামল না। সিপি আই এম এর সেই যুব নেতা আরেকটি ভিডিওর মাধ্যমে আইনসভার কার্যবিবরণী উল্লেখে বোঝাতে চাইলেন যে-না, তৎকালীন সি পি আই এর তিন সদস্য কেউ বাংলা ভাগের প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির সময়ে উপস্থিত ছিলেন না তবে হ্যাঁ, জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ যে ভোট দিয়েছিলেন তা পরবর্তী ভিন্ন অধিবেশনে পশ্চিবঙ্গের ভারতভুক্তি সম্পর্কিত ভোটাভুটির সময়ে-যেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেদিনের আইন সভার কার্যবিবরণী সামনে চলে আসার পরেও মুখ রক্ষায় তাঁর হয়ত আর কিছু বলার ছিলও না, সে বক্তব্য অসার হলেও। প্রত্যাশিতভাবেই সে বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে পালটা একটি ভিডিও প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মহাশয়ও।
এরপরও কোন্ কোন ‘পণ্ডিত’জন ‘ইন্টারেস্টিং’ আলোচনার নামে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অক্ষম চেষ্টা মতামত দিয়েছেন কোন কোন করেছেন ‘ইতিহাসবিদ’ও।
এরপরও কোন্ কোন ‘পণ্ডিত’জন ‘ইন্টারেস্টিং’ আলোচনার নামে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অক্ষম চেষ্টা করেছেন মতামত দিয়েছেন কোন কোন ‘ইতিহাসবিদ’ও।
প্রসঙ্গত ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের (পাকিস্তান) মুসীয় লীগের দাবি ক্রমশ জোরদার হতে জঙ্গী কায়দায় পাকিস্তান আদায়ে জিন্না ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামে’র হুমকী দিয়েছিলেন এবং অবশেষে ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ দিবস পালনের দিন ধার্য হল।।
তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার অন্যতম সদস্য বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মতে ‘ওই সম্মুখসমর (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়; তা ছিল প্রধানতঃ হিন্দুর বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য ছিল ঐ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা আঁৎকে উঠবেন এবং দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান, স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন। (পাক-ভাবতের রূপরেখা)।
আই সি এস অশোক মিত্রেরও পর্যবেক্ষণ-বৃটিশ সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে বঙ্গপ্রদেশ জিন্না ভাগে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যেসাধনে যোগ্য যন্ত্র হবেন সুরাবর্দী ও বারেজ (গভর্নর)। তার কারণ বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ভাবত অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও মোটামুটি সম্পূর্ণ, সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে। তাছাড়া কলকাতা তখনও বৃটিশ শিল্প বানিজ্য ও লগ্নির ঘাঁটি। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শ্রী মিত্রের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে মুসলিম লীগ খুব সযত্নে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসও হয় পুলিশ প্রশাসনের ও উচ্চ কর্মচারীরাও তাদের সঙ্গে গোয়েন্দাবিভাগেও কী ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিশদ বিবরন খবর রাখতেন’। (তিন কৃডি দশ)
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টরাও এগিয়ে এসেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্তের প্রেক্ষিতে বাংলা ভাগেরও দাবি করে। সত্য এ যে জনমত তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সে দাবী তৎকালীন আবহে ছিল সময়ের দাবী। উল্লেখ্য সে বছরের ২২শে এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনমত সমীক্ষায়ও ৯৮.৬ শতাংশ বঙ্গবাসীই বঙ্গবিভাগের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন।
এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ এর ২০শে জুন তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় সংখ্যাধিক্যে (৫৮-২১) পাশ হয় বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব; ফলস্বরুপ পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হলো ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে।
সেই নিরিখে নিঃসন্দেহ ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। উল্লেখ্য সেসময় ভোটাভুটিতে বঙ্গভাগের পক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে ভোট দিয়েছিলেন বামপন্থী সদস্যরাও। ছিলেন তৎকালীন সি পি আই এর দুই সদস্য পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ। এই তথ্যটি হয়ত হজম করতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হয় আজকের ‘বামপন্থীদের’ যাঁরা এবিষয়টি হয় এড়িয়ে যান না হয় গোপন করেন। আর এ প্রসঙ্গে অনেক মনেই এক বিভ্রান্তি জাগে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘যতদূর মনে পড়ে’তে বিধৃত কিছু মন্তব্যে। প্রসঙ্গত আইনসভার ঐ ভোটাভুটির একান্ন বছর পরে স্মৃতিচারন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন আমাদের পার্টি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ও প্রভাব পার্টির ছিল না। (পাতা-৪১) তিনি আরও লিখেছেন- আমাদের পার্টি বঙ্গদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। আমরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গভর্নারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপক পরিষদের শেষ বৈঠক বসল। এই বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। আমাদের পার্টিও বাধ্যহয় বঙ্গদেশ বিভাজনের বাস্তবতা মেনে নিতে। (পাতা-৪২) বঙ্গীয় আইনসভার সেদিনকার কার্যবিবরণী থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সেদিন তিন পর্যায়ে ভোট হয়েছিল তিন পৃথক অধিবেশনে।
সেদিন সকাল এগারোটায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য জেলাগুলি ও হিন্দু সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির সদস্যদের নিয়ে পৃথক পৃথক অধিবেশনের আরম্ভেই যথাক্রমে কিরনশঙ্কর রায় ও ধীরেন্দ্রনারায়ন মুখার্জী যৌথ অধিবেশনের দাবি জানালে বেলা তিনটেয় যৌথ অধিবেশন বসে অধ্যক্ষ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বেই। যেখানে অখণ্ড বঙ্গ প্রদেশটিই চলতি ভারতীয় গণপরিষদে যোগ দেবে না ভিন্ন গণপরিষদে যোগ দিতে ইচ্ছুক এই প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়। উপস্তিত ২১৯ জন সদস্যের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ৯০ জন এবং বিপক্ষে ১২৬ জন ভোট দিলে ১২৬-৯০ ভোটে খারিজ হয়ে যায়। অর্থাৎ উপস্থিত ২১৯ জনের মধ্যে ভোটে প্রদান করেছিলেন ২১৬ জন-তিনজন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন। এরপর ৩-৩৫ নাগাদ একদিকে মুসলিম সংখ্যাধিকা জেলাগুলির সদস্যদের নিয়ে পৃথক অধিবেশন হয় যেখানে ভোটাভুটিতে (যা বাংলা ভাগের প্রশ্নে ছিল না) যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সে তালিকায় নাম নেই তৎকালীন সিপি আই দলের তিন সদস্যের। ।। অর্থাৎ এই ভোটাভুটিতে তাঁরা ভোটদানে বিরত ছিলেন এ সত্য। যদিও একটি প্রশ্নও জাগে-কেন তাঁরা তখন ভোটদানে বিরত ছিলেন? কারণ তাঁরা যদি দেশভাগের ও বাংলাভাগের বিরোধী হয়েই থাকেন, যেমনটি দাবী করা হচ্ছে, তাহলে তো ভোট না এড়িয়ে প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দেবার কথা। তাহলে তাদের ওই আচরণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এ প্রসঙ্গে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বা যুক্তি পাওয়া যায় না।
আবার পরে অমুসলিম বা হিন্দু সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির পৃথক অধিবেশনে বঙ্গভাগ হবে কিনা প্রশ্নে ভোটাভুটিতে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দু’জনেই অন্যান্য হিন্দু সদস্যেদের সঙ্গে বঙ্গবিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন তা সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী থেকেই প্রমাণিত।
এখানে উল্লেখ্য ওই প্রস্তাব ছিল পূর্ব স্থিরীকৃত-শ্যামাপ্রসাদের উত্থাপিত নয়। বস্তুত সেখানে কোন সদস্যের কোন ভাষণ বা নতুন প্রস্তাব পেশের সুযোগ ছিল না। কিন্তু ওই প্রস্তাব সমর্থনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রূঢ় বাস্তবতা অনুধাবনে যে সদিচ্ছা সংহতি ও প্রাজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে সে বিষয়টিও চর্চাযোগ্য। উল্লেখ্য বাংলাভাগের প্রস্তাব সমর্থনকারী ঐ ৫৮ জন সদস্যের নামের তালিকা আছে কার্যবিবরণীর সঙ্গে সংযোজিত তালিকায় (এপেন্ডিকস-বি) (পাতা-৮৫ থেকে ৮৭)। উক্ত এপেন্ডিকস-বি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই তালিকার ৮ নং নামটি হল জ্যোতি বসু এবং ১১নং নামটি রতন লাল ব্রাহ্মণের। প্রয়াত জননায়ক ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত কুমার বসুর নামও আছে তালিকায়- ৭ নম্বরে আর চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নাম ৯ নম্বরে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতা নিকুঞ্জবিহারী মাইতির নাম ১৭ এবং বিপ্লবী বীনা দাসের নাম ১৪ নম্বরে। ২৫ নম্বরে আছে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম; ২৭ নং এ কালীপদ মুখার্জির নাম ৩৫ নং এ নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নাম ৫৭ নং এ আছে কান্দির বিমল সিংহের। উল্লেখ্য ওই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ডি গোমস (৪০), এল আর পেন্টনি (৪৮) আর ই প্লেটেল (৪৯), মিসেস ই এম রিকেটস (৫৪) এবং জি চিডি উইল্কস (৫৮) মতো সদস্যরাও ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। প্রস্তাবের বিপক্ষের ২১ জন সদস্যের নামের তালিকায় কোন অমুসলিম সদস্যে। অর্থাৎ ঐ ফলাফল হয়েছিল সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভাজনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভোট প্রদানে। আজ এ সত্য অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসকে অস্বীকারের নামান্তর। ওই বিবরণী থেকে কোনভাবে প্রতীয়মান হয় না যে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত ছিলেন বঙ্গভঙ্গ করে হিন্দু প্রধান এলাকা ভারতে যোগদান প্রশ্নে ভোটাভুটিতে। সিপিআইএম এর অস্বস্তি হল ওই তালিকায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জ্যোতি বসু নাম থাকায়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে রাজনৈতিক দলের পক্ষেই হোক বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ও প্রায় আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সেদিনের রূঢ় বাস্তবতার ইতিহাস অস্বীকার বা বিকৃত করা কি অনৈতিক নয়।
আজ মিথ্যা প্রচারে, ২০শে জুনের বঙ্গীয় আইনসভায়। অধিকাংশ সদস্যে (যার মধ্যে হিন্দু মহাসভার একমাত্র সদস্য। ছাড়াও বামপন্থীরা সহ প্রায় সব দলের সদস্যরা ছিলেন) সম্মতিতে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই যে বঙ্গবিভাজন। হয়েছিল সে তথ্য অস্বীকার বা কার্পেটের তলায় চালান করে দেওয়ার অপকৌশল চলছে। একদল বলছে ঐ প্রস্তাবের সমর্থনকারী ৫৮ জনই সদস্য নাকি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের লোক। আরেক দল যারা ‘বামপন্থার’ দাবিদার তারা একদিকে বলছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ বা বাংলা তারা চায় না। সেজন্য সমদূরত্ব বজায় রাখতে ঐ প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে ভোটদানে বিরত ছিল এই দু’টি বক্তব্যই যে সর্বৈব মিথ্যা তা সুপরিস্ফুট প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানকারী সদস্যদের তালিকা থেকে। তৎকালীন অবিভক্ত সিপি আই এর এব্যাপারে রাজনৈতিক স্ট্যান্ড যাই থাক না কেন ভোটাভুটির সময় তাঁদের দুই মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন (নিঃসন্দেহে সেদিনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সঠিক ছিল সে সিদ্ধান্ত, যদিও তাঁরা ভোটে অনুপস্থিত থাকলে বা বিপক্ষে ভোট দিলেও প্রস্তাব পাশ হতো) এ দিনের আলোর মত পরিষ্কার যা আজ একথা অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা।
প্রসঙ্গত যে সিলেট গণভোটের প্রস্তাবও ওই অধিবেশনে পাশ হয়েছিল সেই সিলেট গণভোটের সময়েও। সিপি আই এর ঘোষিত স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে জেলা সিপিআই ও জেলা কংগ্রেস পরস্পর এক সাথে সিলেটের ভারতভুক্তির (আসামভুক্তি) পক্ষে কাজ করেছিল। মতাদর্শগত বিরোধ দূরে সরিয়ে রূঢ় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে। যদিও উল্লেখ্য পাকিস্তানের দাবীর তাত্ত্বিক সমর্থক সি পি আই এর (কম্যুনিস্ট নেতা সাজ্জাত জাহীর ও গঙ্গাধর অধিকারীর লিখিত বক্তব্য দ্রষ্টব্য) বঙ্গীয় শাখার নেতৃস্থানীয় জনৈক এবং পরাধীন ভারতে বর্ণহিন্দুবিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। পরে অবশ্য পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় সাজ্জাত জাহীর ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহোদয়দেরও সেদেশ থেকে পালিয়ে এসে সেই ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। একজন মন্ত্রী হয়েও তাঁর উপর ভরসা রাখা দরিদ্র সাধারন স্বজাতিদেরও ত্যাগ করে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে এদেশে পালিয়ে এসে দাখিলি শ্রী মণ্ডলের পদত্যাগ পত্রে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের যে ভয়াবহ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল তাতেই বোধকরি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। ইতিহাসের এও এক নির্মম পরিহাস।
যাহোক ফিরে আসি গোড়ার কথায় ইদানীং রাজনৈতিক তরজায় কিছু পরিসরে প্রেক্ষাপট বিচারে অনীহায় ও অতিসরলীকরণে-হয়ত রাজনৈতিক কারণেও, বঙ্গভাগের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিন্দিত হন। ভারতভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ। কখন এবং কোন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে বাংলাভাগের দাবি উঠেছিল সে ইতিহাসচর্চায় অমনোযোগী এঁরা, এমনকী ভারতভাগের সমর্থকরাও সযত্নে গোপন অথবা সুকৌশলে এড়িয়ে যান রূঢ় সত্যকে। কেউবা আরো এগিয়ে বাংলাভাগের জন্য দায়ী। করতে সবিশেষ উৎসাহী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই।
বস্তুত ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের দাবিতে জঙ্গিপনা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, বিশেষত কোলকাতা কিলিংস ও নোয়াখালিতে একতরফা প্রাণহানি ও রক্তপাতের ঘটনাক্রম যে বঙ্গবিভাজন অনিবার্য করে তুলেছিল, অনভিপ্রেত হলেও, আজ ঠাণ্ডাঘরে বসে আলোচনায় সে সত্য গোপন করে শ্যামাপ্রসাদকে কাঠগড়ায় তুলতে সবিশেষ। ব্যস্ত এবিধ অত্যুৎসাহীরা। প্রসঙ্গত ভাবাবেগের কৌশলে। শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায়কে সাথে পেয়ে যাওয়া সোহরাবদীসাহেব (শরৎবসুর সঙ্গে এবিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির। কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকলেও) তাঁর প্রস্তাবিত ও প্রচারিত ‘অখণ্ডবঙ্গে’র এক স্বর্নীল চিত্র ১৯৪৭ এর ২রা এপ্রিল প্রেসের সামনে উপস্থাপনের পর সংবাদ মাধ্যমের ‘যদি তাঁর। অখণ্ড বঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমান সৌহার্দ্যে বসবাস করতে পারেন তবে অবিভক্ত ভারতে কেন তারা তেমনটি পারবেন না’- এ প্রশ্নে কিন্তু নিরুত্তর থাকেন। বাস্তবিকই এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর কাছে ছিলনা।
আসলে একদিকে ইতিহাস ‘বিকৃতির’ অভিযোগ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হচ্ছে অন্যদিকে বিবিধ উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের ইতিহাস মুছে ফেলার মাধ্যমে এক জনগোষ্ঠীর রক্তঝরা সংগ্রামের কাহিনী গোপন রাখা ও বিস্মরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মরীয়া প্রয়াস চলছে বেশকিছুদিন ধরে, বাংলাভাষী পড়শি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সত্ত্বেও। বাঙ্গালির এক জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের উপাখ্যান ভুলিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা সেই কঠিন সংগ্রামের প্রতি অনুভূতিহীন মস্তিষ্কের এক কৌশলী প্রয়াসের অঙ্গ। কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি তা ইতিহাস থেকে মুছে যাবে?