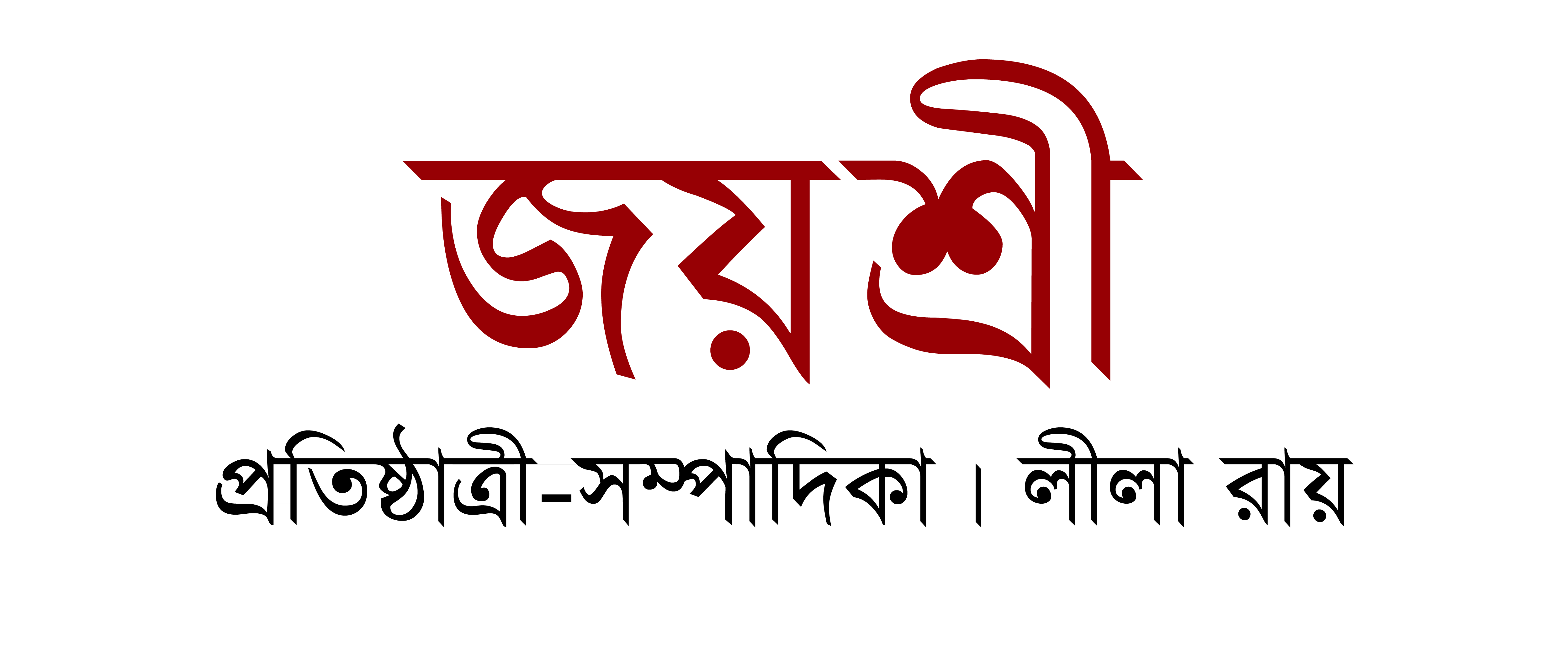শ্রীমতী লীলা রায়,
আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন সুভাষ সম্বন্ধে লিখতে। একটু যদি সময় দিতেন তবে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু আপনি দিনদশেকের মধ্যেই লেখাটি চেয়েছেন। তাই ভাবছি – আমার The Subhash I Knew থেকে কিছু উপাদান নতুন করে লিখে পাঠাই। ইংরেজিতে লেখা স্মৃতিচারণে যা লিখেছি বাংলায় ফের লিখতে হলে একটু-আধটু অদলবদল করতেই হবে। তবে মূল বক্তব্যটির অঙ্গহানি হবে না।
সুভাষ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনি হয়তো জানেন। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে আমি তার কাছে কী গভীরভাবে ঋণী। তাকে আমি যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম সে হল অনুরাগীর চোখ : আর কে না জানে –
অনুরাগের অঞ্জনে মানুষ দেখতে পায় এমন অনেক কিছু যা শাদা চোখে দেখা যায় না। আমার এ-ভঙ্গিকে সুভাষ নিজেই সময়ে সময়ে hero-worship বলে ঠাট্টা করত। কিন্তু আমি ঢিলটির প্রতিদানে পাটকেল ফিরিয়ে দিতাম বলে যে তার নিজের ভালোবাসার মধ্যেও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে পূজার ভাব বরাবরই অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু না, “নিরপেক্ষ” বিশেষণটির উপর আমার একটু বিতৃষ্ণা আছে। আমার মন বলে – নিরপেক্ষ হল উদাসীনেরই অন্য নাম, কাজেই বড়ো সমালোচক সে নয় যে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে বড়াই করে।
এ ভুল বোঝার জগতে এক প্রেমই যা-কিছু নির্ভরযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি জোগায়। এই প্রেমের দৃষ্টিই ফুলে ফলে তত্ত্বদর্শী তথা সত্যদর্শী বলে আদরণীয় হয়ে এসেছে, শুধু তারই এজাহারে মানুষ ভরসা করে গাইতে পেরেছে ‘জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল।’ নিষ্করুণ বিচারকের দৃষ্টি তো বেদরদীর দৃষ্টি – সে কী করে পাবে কোনো কিছুর স্বরূপের দিশা? আমার কাছে চিরদিনই গ্যেটের একটি উক্তি মনে লেগেছে: ‘Aufrichtig zu sein kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber nicht’ অর্থাৎ, আমি আন্তরিক হব এ-কথা দিতে পারি, কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন ভরসা দিই কী করে? গ্যেটে ছিলেন মহামতি মানুষ, একজন বিরল সত্যদ্রষ্টা তিনি দেখেছিলেন যে কাউকে ভালোবাসতে-না-বাসতে আমাদের দৃষ্টি কতকটা বদলে যাবেই যাবে, আর যারা ভালোবাসে নি তাদের চোখে সে-নেকনজর পক্ষপাত মনে হবেই হবে।
সুভাষকে আমি শুধু ভালোবাসা নয় – গভীর শ্রদ্ধা করে এসেছি আকৈশোর। যৌবনে আমার এ-শ্রদ্ধা সত্যিই ভক্তির কোঠায় পৌঁছেছিল। কারণ তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম শুধু দেশভক্ত ত্যাগীকে তো নয় – দেখেছিলাম ভারতের সন্ন্যাসী আত্মাকে যে-আত্মা আধুনিক বাংলাদেশে তার আগে মাত্র দুটি মহাজনের মধ্যে মহিমময় হয়ে ফুটে উঠেছিল : স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। দেশবন্ধুর সঙ্গে তেমন নিকট সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয় নি – ঠিক যখন তাঁর একটু কাছে এসে তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতে শুরু করেছিলাম – আমাকে ডেকেছিলেন দার্জিলিঙে সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশত আমি শিলঙে চ্যারিটি কন্সার্ট দিচ্ছিলাম। কন্সার্ট সেরে তাঁর কাছে যাব যাব করছি, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। সুভাষের কাছে শুনতাম প্রায়ই তাঁর “মৃত্যুহীন প্রাণের” তথা গভীর ভাবধারার কথা। এ-দুটি অমরপ্রাণের একটি অপরূপ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল- খানিকটা গুরু-শিষ্যেরই আদানপ্রদান বলব। দেশবন্ধু বলেছিলেন : “আমার শ্রেষ্ঠ ধন সুভাষকে দিয়েছি – অপেক্ষা করো, তিনি তোমাদের সবই দেবেন।” (পরমহংসদেবও তাঁর তপঃশক্তি স্বামীজিকে দিয়ে এমনি সুরে বলেছেন, “আজ ফকির হলাম।”) অন্য দিকে সুভাষও তাঁকে ভক্তি করত ঠিক যেমন ভক্ত ভক্তি করে দেবতাকে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সে আমাকে মান্দালয় জেল থেকে ২৫ এ জুন, ১৯২৫ তারিখে যে দীর্ঘপত্র লিখেছিল তার খানিকটা অনুবাদ দিই এ কথা প্রমাণ করতে :
“তাঁর বিয়োগব্যথায় আমি মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। আজ স্মৃতির জগতে আমি এ-মহাপ্রাণ মানুষটির এত কাছে আছি যে তাঁর মহৎ গুণাবলীর কথা বিশ্লেষণ করে ফলিয়ে তোলার চেষ্টা করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আশা করি পরে কোনো দিন আমি তাঁর মহত্ত্বের যে-চকিত দর্শন লাভ করেছিলাম তার কিছু আভাস জগৎকে দিতে পারব : এমন আভাস – যা আমি পেয়েছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, তখন তিনি সেকথা আদৌ জানতেন না। আমার মতন আরো অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সত্ত্বেও ভরসা করে লিখতে পারছেন না – পাছে মুখর প্রশংসায় তাঁর লোকোত্তর মহত্ত্বকে ছোটো করে ফেলা হয়।
“তুমি লিখেছ, দুঃখ বেদনার শেষ অবদান যন্ত্রণা নয়। এ কথায় আমার পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু তবু জীবনে অনেক শোকাবহ ঘটনা ঘটে – যেমন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু – যাকে আমি বরণ করে নিতে অক্ষম। আমি ঋষিও নই, ভক্তও নই তাই বড়ো গলা ক’রে বলতে পারি না যে সর্ববিধ যন্ত্রণাই আমার কাছে বরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন আমাকে বারবারই ভাবিয়ে তুলেছে যে, এমন দুর্ভাগাও দেখা যায় না কি (যদিও হয়তো তারা ভাগ্যবান – কে বলতে পারে?) যারা নিয়তির ভ্রূকুটিই সয়ে এসেছে পদে পদে। কিন্তু এই শোচনীয় দুঃখাধিক্যের তর্ক রেখে বোধ হয় বলা চলে যে দুঃখের পেয়ালা নিঃশেষে পান করাই যদি কারো কারো ভবিতব্য হয় তা হলেও খানিকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই তাকে বরণ করে নেওয়া ভালো।
“১৯২২ সালে যখন আমি জেলে যাই তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কুঠরিতেই থাকতাম। আমাদের জেলে একটি কয়েদী আমাদের উঠানে কাজ করত। দেশবন্ধুর স্নেহশীল হৃদয় তাকে বরণ করে নিয়েছিল যদিও সে ছিল দাগী আসামী – এর আগে আটবার জেল খেটেছিল। তা সত্ত্বেও সে অজান্তে দেশবন্ধুর প্রতি ঝোঁকে ও ক্রমশ তাঁকে প্রভুর মতন ভালোবেসে ফেলে। যখন তাঁর কারামুক্তি হয় তখন তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ভক্তটিকে বলেন যে সে জেল থেকে বেরুবামাত্র তার দুষ্কৃতির সহচরদের ছায়া না মাড়িয়ে যেন সোজা তাঁর কাছে চলে আসে। সর্বহারা মানুষটি রাজি হয় ও পরে প্রতিশ্রুতি পালন করে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যে-মানুষ চিরদিন ছিল দুর্বৃত্ত নরাধম সে সেই থেকে আমাদের মহান নেতার আশ্রয়েই আছে, এবং যদিও সময়ে সময়ে সে আজও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তবু মূলত সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও আর পাঁচজনদের মতনই নিরীহ জীবন যাপন করছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে দেশবন্ধুর বিয়োগব্যথা যাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। কেউ কেউ বলে – মহৎ মানুষের মহত্ত্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর ছোটো ছোটো আচরণে, দৈনন্দিন ঘটনায়। এ-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলেও দেশবন্ধুকে মহাত্মা বলতেই হবে – যদি তাঁর বিপুল দেশসেবার কথা বাদও দেওয়া যায়।”
এর উত্তরে সুভাষকে আমি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখতেই সে আমাকে ফের লেখে মান্দালয় জেল থেকে (৯ অক্টোবর, ১৯২৫) :
“দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তুমি যা যা লিখেছ ঠিকই। … আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের সভক্তি প্রেম ও গভীর আনুগত্য দিয়ে বরণ করেছিলাম শুধু এজন্যে নয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম, আরো এই জন্যে যে আমি তাঁকে খানিকটা জানতে চিনতে পেরেছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। এক সময়ে আমরা জেলে ছিলাম একাদিক্রমে আট মাস – তার মধ্যে দুমাস আবার কাটিয়েছিলাম একই কুঠরিতে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।”
সুভাষ এইভাবে নানা সময়েই আমার সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ আলোচনা করত কখনো মুখোমুখি, কখনো বা পত্রের মাধ্যমে। দিনে দিনে তার সঙ্গে এ-সব আলোচনার ফলে আমার কৈশোরের এ-ধারণা আরো দৃঢ় হয় যে তার মহত্ত্বের পরিমাপ করা মোটেই সহজ নয়, যেহেতু সে শুধু কর্মবীর ও দেশনেতাই ছিল না, ছিল উচ্চবিকশিত ধ্যানী, ভক্ত, প্রেমিক যে দেশকে বরণ করেছিল অন্তরের গভীর ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে, মহত্ত্বকে বরণ করেছিল হৃদয়ের উচ্ছল ভক্তি দিয়ে, সর্বোপরি ত্যাগকে বরণ করেছিল তার জন্ম-উদাসী প্রাণের নিবিড় প্রেম দিয়ে। তার নেতাজি রূপের মহিমার কাছে সবাই মাথা নীচু করেছে কিন্তু তার এই ধ্যানী ও ভক্তের রূপ সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। তাই আমি তার একটি ইংরাজি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। এ চিঠিটা সে আমাকে লিখেছিল ভিয়েনা প্রস্থানের পথে জাহাজ থেকে – যখন আমি তাকে আমার এক অপেরা-গায়িকা হাঙ্গেরিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে লৈপিক পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তিনি পরে লিখেছিলেন : সুভাষ যেমন মহৎ তেমনি সরল – আমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে করে… ইত্যাদি। ভিয়েনা থেকে সুভাষ লিখেছিল যে তার অসুখে : ‘She had been an angel to me.’ যাক –
সুভাষ আমাকে জাহাজ থেকে যে-চিঠিটা লেখে সেটি আমার ‘অনামী’-র দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে বলে সবটা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, শুধু তৃতীয় প্যারাগ্রাফটুকুর অনুবাদ দিচ্ছি – যাতে ফুটেছে ওর ধ্যানী ও ভক্তের রূপ। ও লিখেছিল (৫ মার্চ, ১৯৩৩):
‘তোমার একটি পত্রে তুমি আমাকে শিব সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছিলে। বলতে কি, আমার মন কখনো ঝোঁকে এদিকে কখনো ওদিকে – তাই দুর্গা কালী শিব কৃষ্ণ কাকে যে বরণ করব ভেবে পাই না। আমি অবশ্য জানি যে খতিয়ে সবই অভেদ – একমেবাদ্বিতীয়ম্ কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কোনো একটি বিশেষ ভাবরূপের অনুরাগী না হয়েই পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মনের নানা ভাবাবেশে আমি কখনো বরণ করি শিবকে, কখনো কালী বা দুর্গাকে, কখনো কৃষ্ণকে। এদের মধ্যে আবার কখনো চাই শিবকে কখনো শক্তিকে। শিবের পরম যোগী রূপ আমার কী যে মন টানে। হয়েছে কি জানো। সম্প্রতি গত চার-পাঁচ বৎসর হল – মন্ত্রশক্তিতে আমার বিশ্বাস এসেছে – মানে, আমার মনে হয় এক-একটি মন্ত্রের এক-একটি নিবিড় শক্তি আছে। ইতিপূর্বে আমি যুক্তিবাদীদের মতনই মনে করতাম যে মন্ত্র নিছক প্রতীক মাত্র – শুধু আমাদের মনকে সংহত করবার সহায়তা করে। কিন্তু তন্ত্রদর্শন প’ড়ে আমার প্রত্যয় এসেছে যে এক-একটি বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে এক-একটি সহজ শক্তি – আর প্রতি আধারই এক-একটি বিশেষ মন্ত্রের অধিকারী। সেই থেকে আমি ভেবে সারা – আমার আধার কোন মন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি কেননা আমার মন, ঐ যে বললাম, কখনো রঙিয়ে ওঠে শৈবের রঙে, কখনো শাক্তের, কখনো বা বৈষ্ণবের। আমার মনে হয় এইখানেই, গুরু আমাদের পরম দিশারী হতে পারেন কেননা সদ্গুরু আমাদের জানেন আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশি, তাই তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন কে কোন্ মন্ত্র জপ করবে, বা কোন্ পূজারীতি অবলম্বন করবে।’
শ্রীঅরবিন্দ সুভাষের এ-চিঠিটি পড়ে আমাকে লেখেন যে উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই চরিত্রের নানাদিক-থাকেই, তাই তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপের স্বতন্ত্র টান গ’ড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।
সুভাষের জীবন একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে মনে না হয়েই পারে না যে ওর উচ্চবিকাশ হয়েছিল এইজন্যেই যে গ্রহিষ্ণুতা ছিল ওর অসামান্য। তাই নিরন্তর শ্রান্তিহীন কর্মব্রতী হওয়া সত্ত্বেও ওর চিত্তের স্বকীয় অনুসন্ধিৎসা ওকে নিয়তই ঠেলত পরম আত্মজিজ্ঞাসার দিকে। নইলে ওর মতন দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী কিছুতেই গুরুবাদের প্রাণের কথাটি এমন সহজে ধরতে পারত না যে গুরু শিষ্যকে তার নিজের চেয়ে বেশি জানেন ও চেনেন। কিন্তু এ গভীরদৃষ্টির – উপনিষদের ভাষায় ‘ব্যাবৃত্তচক্ষুর’ – উন্মেষ হয় না বহির্মুখী রাজনৈতিকদের, কেননা তাঁদের স্বধর্মই হল আলাদা। তাই সুভাষকে স্বভাবে অধ্যাত্মবাদী তথা ধর্মপ্রাণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আর যে স্বভাবে আত্মসন্ধানী ও অন্তর্মুখী তার সঙ্গে সেই সব অগভীরদর্শী দেশনায়কদের তুলনাই হতে পারে না যাঁরা ভারতের আত্মার খবর রাখেন না, কি যাঁরা মনে প্রাণে বুদ্ধিবাদী বলে মনে করেন যে শুধু সমাজসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক চর্চার ফলেই ভারতের সরাসর চতুর্বর্গ লাভ হবে।
কিন্তু আত্মসমর্পণ বা গুরুবাদের মর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুভাষ কোনোদিনই পরতন্ত্র ছিল না। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনেক সস্তা বুলিই তাকে প্রতিহত করত – আমাদের সাধকদের গতানুগতিকতা, তামসিকতা, স্বাধীনচিন্তার দৈন্য আরো কত কী। আমি এই দিক দিয়ে ওর সংস্পর্শে কম লাভ করি নি – বিশেষ ক’রে যখন পন্ডিচেরি আশ্রমে আমি গুরুবাদের নানা গোঁড়ামিকে তার স্বরূপে দেখতে শিখি নি – যে-গোঁড়ামি ভাবে যে “গুরু গুরু” করলেই পরমার্থ লাভ অবধারিত। পণ্ডিচেরি আশ্রমে এমন কথাও শুনেছি কোনো কোনো বুদ্ধিমান সাধকের মুখে যে আমরা গুরুর চরণে শুধু দণ্ডবৎ করতে পারলেই রাতারাতি অতিমানসের নাগাল পেয়ে অতিমানব বনে যাব – সেকেলে জপ তপ ধ্যান ধারণা ওসব আমাদের মতন এ-যুগের বরপুত্রদের জন্যে নয় – ও সব নিয়ে মাথা বকাক সেইসব মামুলিপন্থী গড়পড়তা সাধক যাদের গুরুও গড়পড়তা বলে জানে না- কেমন ক’রে সুপ্রামেন্টাল যোগে সরাসর সুপারম্যান হতে হয়… ইত্যাদি। এ-ধরনের কথা যখন আমি প্রথম শুনি তখন ভাবি- হবেও বা। কিন্তু সুভাষকে আমাদের আশ্রমের এ-জাতীয় তপস্যাবিমুখ গুরুবাদীদের কথা লিখতে না লিখতে ও আমাকে সাবধান ক’রে দিয়ে সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছিল। ও লিখেছিল (৯ অক্টোবর, ১৯২৫- মান্দালয় জেল) :
‘তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী – আর আমার মনে হয় – স্বামী বিবেকানন্দর চেয়েও গভীর, যদিও স্বামীজির ‘পরে আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দেই যে, ‘নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা’ সময়ে সময়ে দরকার হয় – এমন-কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজ-বিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উদ্ভট কিছু-একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু-চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই হবে সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের ‘double dose’। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি যদি অসাড় না হয়ে যায়, তা হলে নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্য তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমরা যেন ‘sicklied over with the pale cast of thought’ না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়তো সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে – কিন্তু তার চেলারা। গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোনো অনিষ্ট করবে না?’
এ-চিঠি পেয়ে আমার মনে প্রথম দিকে একটু আঘাত লেগেছিল বৈকি, কিন্তু সুভাষের অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল বলে আমি সময়ে দেখতে পেরেছিলাম যে গুরুবাদের যথার্থ রূপটি অনিন্দনীয় হলেও আমাদের জাতীয় তামসিকতার অলক্ষ্য প্ররোচনায় কার্যক্ষেত্রে সে নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কারণে অনেক সময়েই ধামাধরা চেলা-বাদে পরিণত হয়। এইখানে আত্মমনস্ক সুভাষ এ-যুগের নেতাদের মধ্যে ছিল অদ্বিতীয় – স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র বাণীবাহ ও উত্তরাধিকারী যিনি বলেছিলেন জলদনির্ঘোষে (ভাববার কথা- বর্তমান সমস্যা।):
“দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মন্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই – কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষারোপ: বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে, এবং সর্বোপরি, গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্তনে – সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?” কিংবা তাঁর আর-একটি বাণী যা সুভাষ প্রায়ই উদ্ধৃত করত: ‘Worship your Guru, but do not obey him blindly; love him heart and soul but think for yourself. No blind belief can save you.’ (Inspired Talks, পৃ. ১৬৪)
এর পাশাপাশি উদ্ধৃত করি ১৩২১ সালে চব্বিশ বৎসরের যুবক সুভাষের অকুতোভয় ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’- ডাক :
‘আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয় : আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি – দুঃখ দারিদ্র্য নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি, অবিচার, অনাচারের মধ্যে – সবার উপরে, মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।’
এ কি সত্যি রাজনৈতিক নেতার বাণী, না ভারতের আত্মার। মানি, সুভাষ বিবেকানন্দের আত্মার আত্মীয় তথা পতাকাবাহী হয়েও কার্যক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি। আমি এজন্যে একসময়ে যে একটুও আক্ষেপ বোধ করি নি তা নয়, কিন্তু বিশেষ করে সুভাষের আই. এন. এ. সৈন্যদল গঠন করার পরে আমার মনে হয়েছে যে হয়তো এইই ছিল ওর স্বধর্ম, কে বলতে পারে? বলে না- ‘ক্যা জানে কৌন ভেখসে নারায়ণ মিল্ জায়।’ শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছিলাম যে একটা মহত্তর আলো যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন সে চলে খানিকটা অদৃশ্য দেবতার হাতের খেলার পুতুল হয়ে – খানিকটা যেন মুগ্ধাবেশে। ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম দিকে এইভাবেই প্রাণ দিতে ছুটেছিলেন বহু মহাপ্রাণ আত্মবলীদানব্রতী। তাঁদের মধ্যে কারো কারো কাছেও শুনেছি যে অগ্নিযুগে যখন তাঁরা ‘আগে চল্ আগে চল্ ভাই’-এর বহ্নিবাঁশরির ঘরছাড়া ডাক শুনে উধাও হতেন তখন সত্যিই তাঁরা জানতেন না কোথায় চলেছেন কিসের টানে কোন্ সিদ্ধির পথে। শুধু জানতেন – বাঁশি যে শোনে তার উধাও না হয়েই উপায় নেই। সুভাষ যখন সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইম্ফালে হানা দেয় তখন চমকে উঠে এই কথাই মনে হয়েছিল যে ও সর্ববিধ বাধার বাঁধ ভেঙে বীর্যের বন্যাবেগে এভাবে অচিন দুরভিসারে ছুটেছিল শুধু এইজন্যেই যে দেশমাতৃকার মধ্যে ও চাক্ষুষ করেছিল জগন্মাতার মহিমময়ী মূর্তি। নইলে কি ও “দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার” লঙ্ঘন ক’রে “রাত্রিনিশীথে” ভারত থেকে কাবুল, কাবুল থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে ইতালি, ইতালি থেকে মালয়, জাপান বর্মা হয়ে শেষে মণিপুরে হানা দিতে পারত ব্রিটিশসিংহকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলে? মনে হয় ওকে দিয়ে একটা মস্ত ভাগ্যের ও শৌর্যের আদর্শ আমাদের ঘুমন্ত চোখের সামনে ধরতে চেয়েই বিধাতা ওকে গড়েছিলেন জন্ম-অশান্ত ক’রে। ও যদি গড়পড়তা রাজনৈতিক হত তা হলে ওর স্বধর্ম কী সে-বিষয়ে সহজেই একটা কাটাছাঁটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেত। কিন্তু যে-মানুষ মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় – ‘কেবল একটা ব্যক্তি নয়, কোনো একটা প্রচারক মাত্র নয় – যাহার সমগ্র জীবন দেহ মন আত্মা একটা অখণ্ড সত্যের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি’- তার স্বধর্ম স্বভাবস্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞানির্ণয় সুসাধ্য নয়।
একথা অকুতোভয়েই বলা যায় যে তবু সুভাষ যে বহু দুঃখবরণ করে পদে পদে হাজারো বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওর নিয়তিনির্দিষ্ট সত্যসন্ধানে ছুটেছিল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে তার মূলে ছিল ওর অন্তরের এই আলোক-প্রত্যয় যে ওর আন্তরিকতা ছিল নির্ভেজাল।
তাই তো ওর একটি অতি প্রিয় মন্ত্র ছিল শেক্সপিয়রের:
To thine own self be true
And it must follow as the night the day:
Thou canst not then be false to any man.
এ আমার কল্পনামাত্র নয়। সুভাষও ঠিক এই কথাই লিখেছিল ওর পূর্বোদ্ধৃত মান্দালয়ের পত্রের শেষে:
‘আমি একথা মানি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা পেতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভকরে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ’ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোনো কথা নেই, যদি একই আদর্শ হয়তো আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় সবাইকার আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক-না-কেন, আমি কখনোই চাই নে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তা হলে অচিরেই সমগ্র জাতির মধ্যে নব-জীবনের স্ফুরণ হয়। সাধনার অবস্থায় হয়তো মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয় যাতে তাকে বাহিরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাহিরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে; সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব’ দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।’
এই আত্মবিকাশের চিন্তা যার কাছে সত্য, তার ভয় কোথায়? নিজেকে যে ফাঁকি দেয় না সে কি কখনো অপরকে ফাঁকি দিতে পারে? আমাদের এ-তামসিক দেশের আবহাওয়ায় সুভাষ এসেছিল যেন জাগৃতির নিত্যসিদ্ধ পুরোহিত হয়ে। ওর সঙ্গে ১৯৩৭ সালে আমার একটি দীর্ঘ কথালাপের বিবৃতি আমি দিয়েছি The Subhash I Knew বইটিতে। তার শেষের অংশটুকু থেকে একটি উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ-তর্পণের সমাপ্তি টানি -গঙ্গা পূজা হোক গঙ্গাজলে: *
সুভাষ বলল: “জেলে আমি অনেক কিছুই শিখেছি দিলীপ, বিশেষ ক’রে আমার নিজের সম্বন্ধে। কারণ তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে বাইরের জগতের দুয়ার রুদ্ধ হলে আমাদের অন্তরে একটা নতুন জগতের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু তুমি নির্জনবাস বরণ করেছিলে স্বেচ্ছায়- আশ্রমে, আমাকে বরণ করতে হয়েছিল অনিচ্ছায়- জেলে। কাজেই আমাকে পদে পদে লড়তে হয়েছে এই বাধ্য হয়ে বিজনবাসী হওয়ার জন্যে। কিন্তু তা হলেও এই পথেই আমার নিয়তির বিধানে ভগবৎ-বশ্যতার [resignation] মন্ত্রীদীক্ষা হয়, আমি শিখি – দীনতা কাকে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাইরে থেকে দেখলে এ-বশ্যতাকে দুঃখময় মনে হলেও কার্যত আমি খুব বেশি লাভ করি – নিজেকে এই দুঃখের আলোয় আবিষ্কার ক’রে। তুমি খানিক আগে বলেছিলে – তুমি আত্মসমর্পণ কাকে বলে জানতে পেরেছ অনেক দুঃখ পেয়ে তবে। আমি বলতে পারি না সে কথা। তবে আমার ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্নটাই ওঠে না, যেহেতু আমাকে চিরদিন লড়তে হয়েছে আমার মধ্যেকার এক আন্তর বিদ্রোহের সঙ্গে – যে আমাকে কখনো দুদণ্ডও স্বস্তি দেয় নি। তাই তো আমি জেলে আসতে-না-আসতে প্রতিবারই অসুখে পড়েছি – স্বাস্থ্যরক্ষার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু উপায় কী? আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম জেলে আসতে-না-আসতে – সময় যে ব’য়ে যায় – বলত মন, আর ব্যথায় পড়তাম আমি মুহ্যমান হ’য়ে।’
সুভাষ চিন্তিত মুখে বলে চলে: ‘আমার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু আমি করি কী? আমার তো এমন কোনো গুরু নেই যে আমাকে পথের নির্দেশ দেবে। অগত্যা আমি নিজেকে নিরীক্ষা করতে শুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক’রে আবিষ্কার করলাম যে পথচলায় সব চেয়ে বড়ো দিশারী হচ্ছে বাইরে অপরের সম্বন্ধে তিতিক্ষা – charity, আর অন্তরে বিনম্রতার সাধনা – humility। এরা উভয়ে আমার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে অপরকে রুক্ষ হয়ে বিচারের নাম অবিচার কেননা আমরা সবাই কমবেশি অন্ধ ও অজ্ঞান-কাজেই দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি আরো একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম: যে আমরা যে দুর্বল এটা খতিয়ে উপলব্ধি করতে-না-করতে বল এসে যায়।
‘প্রতি উপলব্ধির সঙ্গেই আসে পরিবর্তন। আমার মধ্যে এই পরিবর্তনের পরে আমি কৃতসংকল্প হলাম যে আমাকে সব আগে নিজের কাছে খাঁটি হতে হবে, ‘to thine own self be true’ মন্ত্র জপ করে। এর মানে কী! না, আমি নিজের প্রতি কাজকে তেমনি ভাবে ওজন ক’রে ক’রে দেখব যেমন ভাবে দেখি আর সবার কাজকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে শুধু যে আমাকে সহিষ্ণু – lenient- হতে হবে তাই নয়, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে।’
সুভাষ থেমে ঈষৎ করুণ হেসে বলে চলল : ‘তোমাকে আশা করি বলতে হবে না যে আমি হাড়ে হাড়ে জানতাম যে কর্তব্য কী তার দিশা পাওয়া আর সে-কর্তব্য পালন করা এক জিনিস নয় – ঠিক যেমন কোনো কিছু কামনা করা আর তাকে হাতে পাওয়া এক জিনিস নয়।… আমার কৈশোরে আমি পড়েছিলাম বুদ্ধের বিখ্যাত বাণী যে সবাইকে তেমনি ভালোবাসতে হবে যেমন বাসে যা তার একটি মাত্র সন্তানকে। বেশ মনে আছে – যখন এ-কথা প্রথম পড়ি তখন আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় উঠে চলতাম – মাটিতে পা পড়ে না অবস্থা। কিন্তু হ’লে হবে কী, সংসারকে যতই দেখতে বুঝতে চিনতে শিখি ঠিক কি সেই অনুপাতেই ভালোবাসবার শক্তি আসে ক’মে – মানে অবশ্য যে-ভালোবাসার কথা বুদ্ধ বলেছিলেন।’
সুভাষের মুখে ফের আত্মমনস্ক হাসি ফুটে ওঠে : ‘কিন্তু দিলীপ, জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর হতে-না-হতে আমরা পদে পদেই ঠেকে শিখি না কি যে, কোনো বড়ো উপলব্ধির পথই কুসুমাবৃত নয়। তুমি গুরুবাদের পথ বেছে নিয়েছিলে। আমি অকপটেই স্বীকার করছি যে অনেকদিন ধরেই আমার মনের সংশয় কাটে নি – তুমি ঠিক পথে চলছ না ভুল। কিন্তু আট বৎসর বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হতে-না-হতে আমার সব সংশয় কেটে গেছে। গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করতে হয় – (আর এর চেয়ে গভীর বিচার আর কীই বা হতে পারে?) – তা হলে কিছুতেই বলা চলে না যে তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলে। পথচলায় আমি যদি সহিষ্ণু ও তিতিক্ষাশীল হতে শিখে থাকি তা হলে তুমি কী শিখেছ – বলব খোলাখুলি। আচ্ছা শোনো।’
একটু থেমে সুভাষ বলে চলল ফের একটানা : ‘সেদিন অনেক রাত অবধি তুমি আমার কাছে না রেখেঢেকেই বললে তোমার নানা অগ্নিপরীক্ষার কথা, দোলার কথা, দুর্বলতার কথা। আমি খুব মন দিয়েই শুনছিলাম – কি যে দেখছিলাম – ওজন করছিলাম তোমার প্রতি কথার নিহিতার্থ। তুমি ঘটা করেই বললে তোমার নানা সংশয়ের কথা; নিরাশার কথা – এমন-কি তোমার নানা প্রবর্ধমান অবিশ্বাসের- Cynicism-এর- কথাও তুমি বললে খোলাখুলিই। কিন্তু একটিবারও তুমি তোমার গুরু কি ইষ্টের সম্বন্ধে এমন কোনো কথা বলো নি যাকে বলতে পারি disloyalty: তাই তুমি যতই বলো-না-কেন, আমাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করাতে পারো নি যে তুমি বিশ্বাসে প্রত্যয়ে দেউলে – একটিবারও তুমি আক্ষেপ করো নি সংসারে নানা ভাবে সফল হবার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলে ব’লে। এর পরে আমি কেমন করে তোমার নিজের সম্বন্ধে এ-রায়ে বিশ্বাস করি বলো যে তুমি স্বভাবে সন্দিগ্ধ- sceptic। না, তোমাকে বেশি বিব্রত করতে চাই না – অন্য প্রসঙ্গ পাড়ছি এখুনি – কেবল একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছিলাম কবি য়েট্স্-এর একটি চমৎকার উক্তি: যে, ভগবান মানুষকে অনেক কিছুই বর দিতে পারেন বটে, কিন্তু মানুষ তাঁকে দিতে পারে একটি মাত্র উপহার: বিশ্বাস। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম কথাটি পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে খৃস্ট সাধারণ মানুষকে – Scribes ও Pharisee-দেরকে বিশ্বাসে দীন ব’লে দেগে দিয়ে তাদের পরে একটুও অবিচার করেননি। এ যুগের মানুষ সম্বন্ধে কি তার ভর্তসনা আরো বেশি খাটে না? এক কথায় সংসারে সবচেয়ে বড়ো পাথেয় হল বিশ্বাস। তাই দিলীপ, আমার মনে সময়ে সময়ে প্রশ্ন জাগে আমি আমার প্রতিপক্ষকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারব এ-বিশ্বাস আমার সত্যি আছে তো? কিন্তু-”ব’লে ও ফের একটু থেমে বলল-”যে-পথেই চলি-না-কেন হার না মেনে শেষ পর্যন্ত চলা কঠিন না হয়েই পারে না। নয় কি?”
সুভাষের একটি অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল নিবেদিতার The Master As I saw Him. বিলেতে সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত এ-বইটিতে স্বামীজির নানা মতামত। এদের মধ্যে একটি উক্তি ছিল ওর বিশেষ প্রিয়। নিবেদিতা লিখেছেন:
To the Swami it was only natural to say in answer to an enquirer. “Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet, not with my tears but with my heart’s blood.’ (পৃ. ২৮৭)
এর পরেও সুভাষকে ‘চিরন্তনের তীর্থযাত্রী’ উপাধি দিলে কি খুব ভুল হবে?
মাঘ ১৩৬৫
*বলা বাহুল্য এ-অনুলিপি তার মুখের কথার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়- তা ছাড়া আমার নিজের ভাষায় বলা। তবে এ বিষয়ে সে নানা সময়ে নানাভাবেই ফুটিয়ে তুলত তার নানা স্বপ্ন ঘন্য সত্যজিজ্ঞাসা। তাই ভাষা আমার হলেও বক্তব্যটুকু তারই একথা বলতে পারি অকুতোভয়েই।