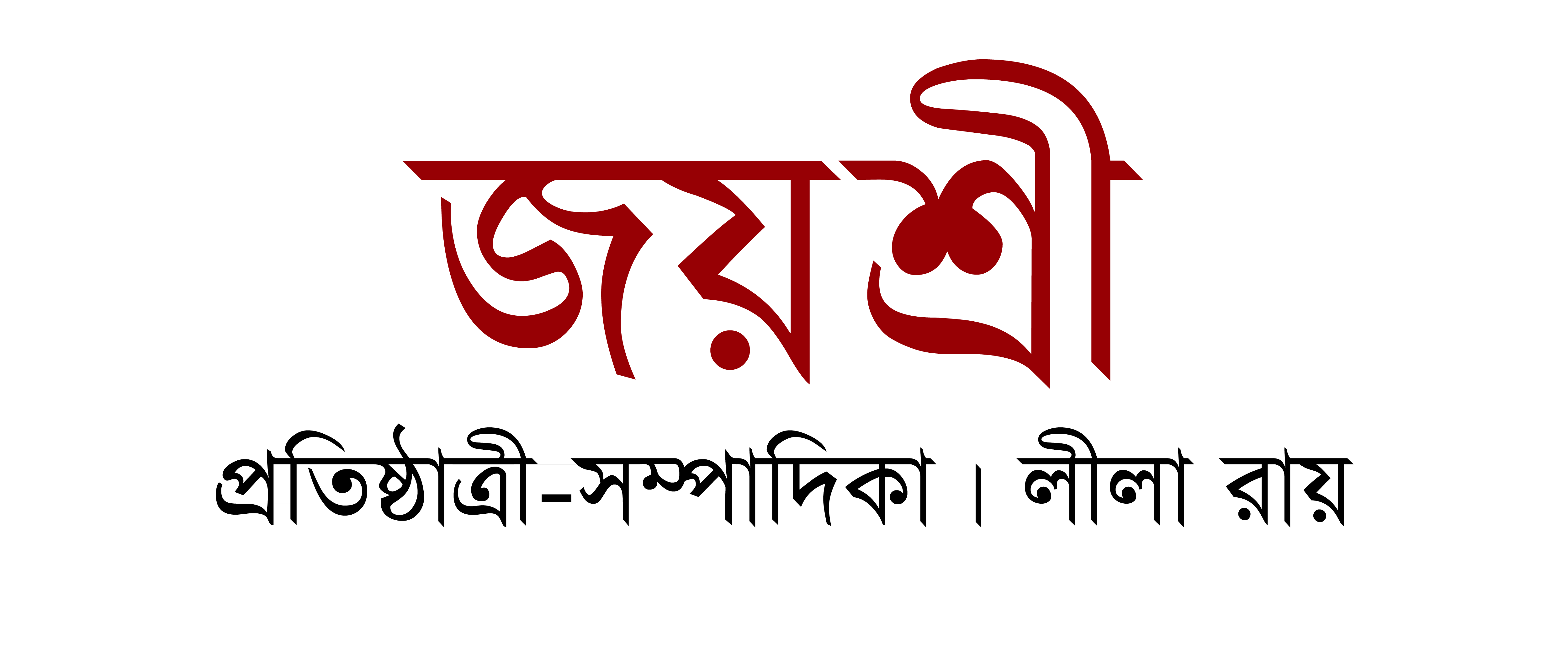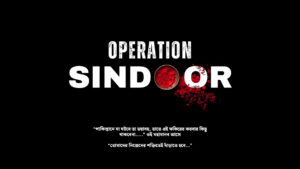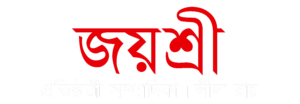রমেশচন্দ্র মজুমদার
কিছুদিন পূর্বে হরিদ্বার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম ঠিক ব্রহ্মকুণ্ডের ধারেই গঙ্গাতীরে যে বিশাল বাঁধানো চত্বর, তাহার মাঝখানে নেতাজীর দণ্ডায়মান প্রস্তর মূর্তি। ইহা জনৈক অনুরক্ত অথবা ভক্ত দেশবাসীর দান। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর শহরে গিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে যে প্রশস্ত রাস্তাটি শহরের দিকে গিয়াছে তাহা দিয়া একটু অগ্রসর হইলেই যে চৌরাস্তার মোড় তাহার মধ্যস্থলেও নেতাজীর প্রস্তরমূর্তি। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্য পর্বতের অপর পার পর্যন্ত নেতাজীর প্রতি দেশবাসীর এই সম্মান ও ভক্তির চিহ্ন দেখিয়া মনে যথেষ্ট গর্ব ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। নেতাজী ব্যতীত তাঁর সমকালবর্তী আর কোনো বাঙালি বাংলার বাহিরে এরূপ বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইতে পারেন নাই – আর কাহারও প্রতি ভারতবর্ষ এইরূপ সম্মান দেখায় নাই। বাংলার অধঃপতনের দিনে এই কথাটাই বারবার মনে পড়িল। আজ বাংলায় এমন একজন ব্যক্তিও নাই বাংলার বাহিরে রাজনীতিক্ষেত্রে (অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে) যাহার বিশেষ কোনো প্রভাব আছে। অথচ ইহার পূর্বে শতাব্দীরও অধিককাল বাংলার আকাশে যে-সকল জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল তাহাদের আলোকে ভারত আলোকিত হইয়াছে। রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু একে একে সে-সব দেউটি নিবিয়া গিয়াছে। সর্বশেষ ছিলেন নেতাজী। তিনিও সম্ভবত ইহলোকে নাই। বাংলার এই সর্বশেষ কৃতীপুরুষের সম্মান দেখিয়া একদিকে যেমন আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি-অন্য দিকে তেমনই হতাশা নিরানন্দ ও অবসাদে হৃদয় ভরিয়া যায়। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর বাঙালির অবস্থা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিই বার বার মনে পড়ে-
“হে সাত কোটি সন্তানের মোহনীয় মা।, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করো নি।”

নেতাজীর ব্যক্তিত্ব চরিত্র অথবা জীবনীর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল যাহা বাঙালি (অথবা ভারতীয়) চরিত্রে দুর্লভ। অনমনীয় স্বাধীনতা-প্রীতি ইহার অন্যতম। স্বাধীনতার জনা অনেক ভারতীয় প্রাণ দিয়াছেন- সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন- বহু লাঞ্ছনা ও যাতনা সহ্য করিয়াছেন সে বিষয়ে নেতাজীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতেছিনা। কিন্তু জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই একটি প্রনবতারার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করা, হতাশার ঘোর অন্ধকারেও বিচলিত না হইয়া ঐ লক্ষ্য সাধনের জন্য নূতন নূতন পথের সন্ধান করা, মহাত্মা গান্ধীর যুগে নিছক অহিংসাবৃত্তির আদর্শ পরিহার করিয়া ভারতের মুক্তির সন্ধানে অন্য পথের উদ্ভাবনায় তৎপর হওয়া, বর্তমান জগতের পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করিয়া তাহার সাহায্যে ভারতের উন্নতির পরিকল্পনা এবং এই কল্পনা সার্থক করার জন্য অদম্য উৎসাহ, অভূতপূর্ব সংগঠন শক্তি, পরাক্রান্ত বিদেশী জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন, অকুতোভয়ে বিপদসংকুল সাবমেরিনে সুদূর সমুদ্রযাত্রী- এই সকল স্মরণ করিলে তাঁহার চরিত্রগত যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই তাহা ভারতে দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন- নিবিড় অরণ্য মধ্যে অন্ধকারে মহাপুরুষের প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলিলেন তিনি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। তখন মহাপুরুষ বলিলেন ‘প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে।’ সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন আর কি আছে- আর কি দিব? উত্তর হইল ‘ভক্তি’। নেতাজী এই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।
বাঙালিরা ভাবপ্রবণ, তাঁহারা কথায় পটু কিন্তু কোনো একটা বড়ো জিনিস গড়িয়া তোলার শক্তি নাই- এ
অপবাদ প্রায়ই শুনিতে পাই, এবং ইহা যে একেবারে অমূলক ইহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু নেতাজী ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি ও পরিচালনায় তিনি যে গঠনশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষ নহে, সমস্ত জগতে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রকৃতভাবে কখনো লিখিত হয় তবে নেতাজীর জীবনের এই অংশ তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অভিযান ব্যর্থ হইলেও ইহা যে ইংরেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের একটি প্রধান কারণ ইহা বহু পূর্বে অন্য একটি বাংলা প্রবন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। শুনিয়াছি এই প্রবন্ধ কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রীতিকর হয় নাই- ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া সরকারি দপ্তরে পাঠানো হইয়াছিল এবং ইহার জন্য সরকারি কালো খাতায় (Black Book) আমার নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে ইহার জন্য আমার অসুবিধা ও অপকারও হইয়াছে, বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে এ কথাও শুনিয়াছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে দিল্লীর বিরাট উৎসবে ঘণ্টার পর ঘণ্টাব্যাপী ভাবোচ্ছ্বাসপূর্বক বক্তৃতার মধ্যে একবার মাত্র নেতাজীর নামোচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তাও যাঁহারা অনুভব করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য উল্লিখিত আচরণ অসংগত নহে। কিন্তু তথাপি আমি এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে নেতাজী সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে আমি যে মত
ব্যক্ত করিয়াছি তাহার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তাহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমার পূর্বমত আরও দৃঢ় হইয়াছে।
তবে এ কথা আমার স্বীকার করা উচিত যে নেতাজীর সম্বন্ধে আমার মতামতে কিছু পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে। কারণ সুভাষচন্দ্রকে আমি বাল্যকাল হইতে জানি। আমি যখন কটকে স্কুলে পড়ি তখন সুভাষচন্দ্র কটকে থাকিত এবং আমার এক ভাগিনেয় তাহার সমবয়সী বন্ধু হওয়ায় আমাদের ওখানে আসিত। সেই অবধি বরাবরই জানাশোনা ছিল- তবে আমাদের জীবনের গতি পৃথক হওয়ায় ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। বিশেষত তাহার রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্কে আমি দূরে দূরেই থাকিতাম। তবে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি চিরদিনই অক্ষুন্ন ছিল। ইহার পরিচয়স্বরূপ সুভাষচন্দ্রের সহিত আমার শেষ সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাহার সর্ব শেষ ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বকার ঘটনা বলিয়াই ইহার বিবরণ দিতেছি।